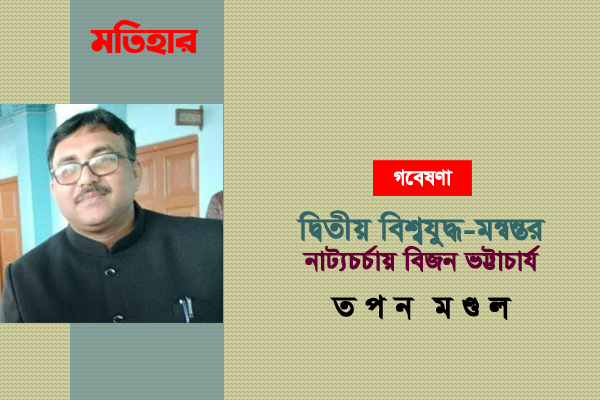সময়টা তখন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫)। একই সময় চলছে পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের পালা। বিয়াল্লিশের বিপ্লব। ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই সময় বাংলায় নেমে এল তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৯৪৩ সাল। এ মন্বন্তর ছিল ১১৭৬-এর মন্বন্তরের চেয়েও ভয়াবহ। তাই অনেকেই OSU Jerseys deion sanders jersey OSU Jerseys purdy jersey Ohio State Team Jersey rowan university new jersey florida jersey College Football Jerseys Ohio State Team Jersey College Football Jerseys Florida state seminars jerseys detroit lions jersey,green bay packers jersey,eagles kelly green jersey,jersey san francisco 49ers deion sanders jersey brandon aiyuk jersey custom ohio state jersey একে ‘মহামন্বন্তর’ নামে আখ্যা দিয়েছেন। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস যখন মুখরিত, পথে পথে মৃত মানুষের স্তূপ—তখন বাংলার হাজার হাজার গ্রামের বুক জুড়ে নেমে এল মহাশ্মশানের নীরবতা। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে—মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছে না- আপনজনেরাও ক্ষুধার তাড়নায় ও বাঁচার তাগিদে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী—কারো প্রতি কারুর আস্থাvm 1986 trøje tomnanclachwindfarm.co.uk ribstol elan ribstol elan bundy kilpi damske dymytr povlečení sevilenotocekici.com sevilenotocekici.com red-gricciplac.org skrue kasse tomnanclachwindfarm.co.uk skrue kasse stenyobyvaci.cz bundy kilpi damske ribstol elan নেই।
এখন প্রশ্ন হলো, কেন এমনটা হলো? প্রথমত, বলা যেতে পারে ১৯৪২ এর ১৬ অক্টোবর দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও প্রচণ্ড colleges in new jersey brandon aiyuk jersey custom ohio state jersey brandon aiyuk jersey justin jefferson lsu jersey johnny manziel jersey florida state football jersey Ohio State Team Jersey brandon aiyuk jersey custom football jerseys penn state football jersey penn state jersey detroit lions jersey,green bay packers jersey,eagles kelly green jersey,jersey san francisco 49ers custom ohio state jersey oregon ducks jersey বৃষ্টিপাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। চাষিরা ফসল উৎপাদনে বড় রকমের একটা ধাক্কা খায়। এছাড়া আউশ ধান ও আমন ধান পরপর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় ফসল উৎপাদনে চাষীরা ভালো ফল পেল না। খাদ্য শস্যে ঘাটতি দেখা দিল।
দ্বিতীয়ত, এই সময় চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বাংলাদেশে দলে দলে বাইরে থেকে সৈন্য আসছে। এদিকে যুদ্ধের উপকরণ তৈরীর জন্য কারখানাও গড়ে উঠছে। সেখানে অবাঙালি শ্রমিকের আগমনে কারখানা ভরে উঠছে। প্রয়োজন বাড়তি খাদ্য শস্যের। অপরদিকে জাগান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করেছে, ফলত ভীত সন্ত্রস্ত অসংখ্য মানুষ ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিচ্ছে—এ সমস্ত বাড়তি মানুষের জন্য প্রয়োজন খাদ্যের যেখানেই খাদ্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে ১৯৪২-এর ১০ মার্চ জাপানের অধিকারে ব্রহ্মদেশ চলে গেল—তখন থেকে খাদ্য সংকট আরো প্রবল হল। কারণ, ব্রহ্মদেশ থেকে বাংলাদেশে ততদিন যে খাদ্যশস্য আমদানি হত তাও বন্ধ হয়ে গেল। স্বাভাবিক কারণে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। এছাড়া হয়ত ততই সংকট দেখা দিত না যদি কিনা আমাদের দেশের অতিলোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভের আশায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করতো।
বাংলাদেশে অসাধু ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন, জোতদারেরা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, স্বল্প-উৎপাদন, যুদ্ধ ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করল। এছাড়া বিত্তবান গৃহস্থরা ভবিষ্যত ভেবে পারিবারিক নিরাপত্তার কারণে শস্য মজুত করতে শুরু করুন। এমনকি খাদ্য সংকটের পূর্বাভাস পেয়ে হিসেবী মানুষরা শহর কলকাতাকেন্দ্রিক ভবিষ্য ভাবনা করলেন কিন্তু গ্রাম বা জেলাভিত্তিক কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে করা হল না। সুতরাং এক সময় খাদ্য সংকট যখন তীব্র আকার ধারণ করল তখন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হল এবং ফলভোগ করল বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের সাধারণ মানুষেরা বলা যেতে পারে, এক প্রকার মানুষের স্বার্থপরতায় তেরশ পঞ্চাশে বাংলাদেশে মন্বন্তর নেমে এল। যাকে বলা যায় – man made crisis। এর ফলে প্রথমেই খাদ্যদ্রব্যে আক্রান্ত হল সাধারণ ছা-পোশা মানুষেরা। দেখা যায়, ১৯৪২-এর ১১ ডিসেম্বর যে চাল ছিল ১৩/১৪ টাকা মণ, সেই চাল ১৯৪৩ এর ১২ মার্চ নাগাদ তা হয়ে গেল ২১ টাকা মণ। আবার মে মাসের দিকে সেই চাল ৩০ টাকা মণ ছাড়িয়ে গেল। ১৯৪৩ এর আগস্ট মাস নাগাদ চালের দাম বেড়ে হয়ে গেল ৩৭ টাকা, (প্রতি মণ)। অক্টোবর মাস নাগাদ একই চাল চট্টগ্রামে ৮০ টাকা (প্রতি মণ) এবং ঢাকায় ১০৫ টাকা দর গিয়ে দাঁড়াল। সুতরাং এ থেকে খুবই স্পষ্টত যে, পয়সা দিলে খাদ্য দ্রব্যের অভাব নেই। অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশি পয়সা রোজগারের ধান্দায় বাজারে কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করে চলেছে।
ফলত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্বচ্ছ উপার্জনের পরিবারে স্বভাবত অভাব অনটন শুরু হয়ে যায়। দিন মজুর, কৃষকরা তাদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত পেটের জ্বালায় জোতদার, সুদখোর মহাজনদের কাছে বিক্রি করে অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। শুধু বাঁচার তাগিদে। শ্রমজীবি চাষী মুটে মজুর পরিবাররা প্রথমে অর্ধাহারে তারপরে অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মারা গেল। বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তর কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলো। অবশেষে মহামারী দেখা দিল। মৃত্যু হল অসহায় গরীব মানুষের। হাজার হাজার মানুষ সাতপুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ করে শুধু বেঁচে থাকার আশায় গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি দল। ক্রমশ গ্রাম জনশূন্য হয়ে যেতে থাকে। শহরে যাওয়ার পথে বহু মানুষ অর্ধাহারে-অপুষ্টিতে বা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। শহরে তাদের আর ইহজনমে যাওয়া হল না। যারাই বা গেল- তাদের অনেকেরই শহরে মৃত্যু হল – সুদিনে গ্রামে তাদের আর ফেরা হল না। আমরা জানি, গ্রামীন এই ক্ষুধার্ত মানুষ কলকাতা মহনগরীতে সবচেয়ে বেশি ভীড় জমায়। কারণ, কলকাতার কাছাকাছি জেলাগুলিতে সর্বপ্রথম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বলাবাহুল্য, দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল ১৯৪৩- এ। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপ্তিকাল মোটামুটি ১৯৪২-এর শুরু থেকে ১৯৪৪-এর শেষ অবধি। কাজেই এই সময়কে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করে নিতে পারি:
প্রথম পর্ব-১৯৪২-১৯৪৩, মার্চ পর্যন্ত। (এই সময় দুর্ভিক্ষ হয়নি।
দ্বিতীয় পর্ব-১৯৪৩(মার্চ)-১৯৪৩ (নভেম্বর) – (এই সময় ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মরতে শুরু করেছে।)
তৃতীয় পর্ব–১৯৪৩ (নভেম্বর)-১৯৪৪ পর্যন্ত – (দুর্ভিক্ষের সংকট কাল শেষ-মানুষের মৃত্যুর টল।)
এই সময় কালে কলকাতা মহানগরীর রাস্তায় দু’পাশের ফুটপাতে গ্রাম থেকে আসা ক্ষুধার্ত মানুষে ছেয়ে গেল। সরকারি লঙ্গরখানায় একবেলা খিঁচুড়ি খেয়ে মানুষ বাঁচার আশায় বুক বেঁধে পড়ে আছে। এছাড়া শহরে ধনবান বাবুদের দরজার দরজায় একমুঠো ভাত অথবা একটু ফ্যানের জন্য তারা পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে থাকল। অবিভক্ত বাংলায় এই দুর্ভিক্ষে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল— চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলি। এছাড়া মাঝারি ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত হল-যশোর, খুলনা, বরিশাল জেলা। অল্পস্বল্প ক্ষতি হল-রংপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া ও দার্জিলিং জেলা। অধিক ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়ে অবশেষে কলকাতার পথে এগিয়ে এসেছিল একমুঠো খাবারের আশায়। একটু ফ্যান, একটু ভাত অথরা কলকাতায় সন্তায় রেশনের চাল ও আশ্রয় পাবার আশায়। গ্রামগুলি ক্রমশ জনমানবশূন্য হয়ে যায়।
শহরে এসে প্রথমে তারা কাজ খুঁজতে থাকে, উপযুক্ত কাজ না মেলায় অবশেষে দরজায় দরজায় একটু ভাত, একটু ফ্যানের জন্য ভিক্ষা করে বেড়ায়। ফুটপাতে ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খায়। খাবারের জন্য কুকুরে-মানুষে মারামারি, এমনকি মানুষ কুকুরের কামড় খেয়ে রক্ত ঝরায়। এই অসহায় মানুষেরা মান-সম্মান, বিবেক, ধর্ম সব খুইয়ে পথের ভিখারি হয়ে যায়। অথচ তারা কেউ পেশাদার পথের ভিখারি নয়- [ পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে পথের ভিখারি হয়েছে তারা। সমকালের এইসব পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র পাই সেসময় লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাট্যসাহিত্যে। এছাড়া সেদিনকার পত্র পত্রিকার বিবৃতি আজও আমাদের কাছে বাস্তব দলিল হয়ে আছে। প্রসঙ্গত আমরা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের লেখা দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত একটি বর্ণনার কথা বলতে পারি,
“রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। চৌরঙ্গী, কালিঘাট, লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়। সর্বত্র একদৃশ্য— শত সহস্র কঙ্কাল যেন ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে চিৎকার করছে। পেটের জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও জগদ্ধাত্রী কৃষানী দু’মুঠো অন্ন ভিক্ষা চশইতেও সাহস পায় না—বলে ফ্যান দাও। মনুষ্যত্বের কী অবমাননা। গরু-ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে কাড়াকড়ি। ডাস্টবিনে পচা এঁটোকাটা নিয়ে কুকুরে মানুষে মারামারি। আর দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে।” (ক্ষুধার্ত বাংলা-চিত্তপ্রসাদ)
এই সময় ‘স্টেটস্ম্যান’ পত্রিকায় ফ্রেনহস্ অ্যাম্বুলেন্সে ইউনিটের এক সদস্য মাননীয় সুধীর ঘোষ একটি চিঠি লিখেছিলেন, -(স্টেট্সম্যানকে) তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন—
“গত দুসপ্তাহের মধ্যে এমন কোন দিন যায়নি যেদিন আমি পথে মৃত দেহের স্তূপ দেখিনি। শহরের পথঘাট সব রকমের সংক্রামক রোগাক্রান্ত ভিখারীতে ভরে গেছে। মৃতদেহের সৎকার করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অবস্থা আরও ভয়াবহ। ম্যালেরিয়া ও অনাহারে দলে দলে মানুষ মারা যাচ্ছে। মৃতদেহ দাহ করবার মত যথেষ্ট সংখ্যক লোক নেই, কাজেই প্রায়ই মৃতদেহগুলোকে খালের জলে ঠেলে ফেলা হয়। ম্যালেরিয়া ও অনশনে কাঁথি জনশূন্য হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।”
এমতাবস্থায় দুর্গতদের সাহাযার্থে নানা জায়গা থেকে সাহায্য আসতে শুরু হল। বোম্বাই, করাচী, কাশী, পাটনা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ থেকেও অর্থ সাহায্য পাওয়া গেল। সুদূর অ্যায়ারল্যান্ড থেকেও দুর্গতদের জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া গেল। বাংলার বাইরে থেকে খাদ্যশস্য এলো। যদিও তার অধিকাংশ কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন হয়ে গেল। সেনাবাহিনীদের দ্বারা ত্রাণকার্য সম্পন্ন করা হল। ১৯৪৩-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৭০, ০০০ টনেরও বেশি খাদ্যশস্য বিতরণ করা হল। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অন্নসত্র খুলে খিচুড়িধ, চাল বাজরা, জোয়ার, ডাল ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী বিতরণ শুরু হল। বলাবাহুল্য, কলকাতা শহরে সে সময় অর্থাৎ ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাস নাগাদ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। এই সব মানুষদের সেবা করার জন্য কলকাতা কন্ট্রোলের দোকান থেকে ছ’আনা সেরে মানুষ পিছু দু’সের করে চাল দেওয়া শুরু হল, ১৯৪৩-এর মার্চ মাস থেকে। দেখা যেত, দোকানগুলিতে চাল নেবার জন্য রাত থেকে বড় বড় লাইন পড়ে আছে—সকাল হলে চাল পাবে। পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও যেদিনে ক্ষুধার জ্বালায় চাল নেবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকত। এমনকি বহুনারী ক্ষুধার জ্বালায় সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছিল। আদর্শ ও নীতিবোধে যেদিন ফাটল ধরে গেল। গ্রাম-শহরের চোরা কারবারিরা সেদিন নারী পাচারের ব্যবসা করে মুনাফা লুঠতে শুরু করল। শুধু খাদ্য দ্রব্য নয়, বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস মজুত করে কালোবাজারীরা মুনাফা লুঠতে শুরু করল। এর পিছনে অবশ্যই সেদিনের ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ঔদাসীন্য অনেকটাই দায়ী। যাই হোক, সেদিনে সরকারি সাহায্য, শিক্ষিত সমাজসচেতন মানুষের সার্বিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মন্বন্তরে প্রাণ হারাল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। ‘ফেমিন ইনকুয়ারী কমিশন ইন্ডিয়া’র রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় পনের লক্ষ মানুষের সেদিন মন্বন্তরে প্রাণ দিতে হয়েছিল।
মন্বন্তর সম্পর্কে সমকালের কিছু পত্র পত্রিকার প্রতিবেদন আমাদের প্রসঙ্গত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৩-এর ২০ অক্টোবর জনযুদ্ধ পত্রিকার প্রতিবেদন –
২৪ পরগণার “মসাট ইউনিয়নে ১২০০০ লোকের বাস, কিন্তু তার মধ্যে ১৫০ জনের বেশি দুবেলা খাইতে পায় না। শতকরা ৫০ জন রিলিফ কিচেনে খায়। ক্ষুধার জ্বালায় স্ত্রীলোকেরা বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। পরে যখন তাদের গ্রামে রিলিফ কিচেন খোলা হইল, তখন আবার তারা গ্রামে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাদের স্বামীরা তাদের অনেককেই ঘরে ফিরিয়া লইল না, তারা আবার আশ্রয় লইল রাস্তায়। খোলা মাঠে ছেলে মেয়ে নিয়া পড়িয়া থাকে। ছোট শিশুকে শেয়ালে টানিয়া লইয়া যায়।
(মেদিনীপুর)—২০ অক্টোবর, ১৯৪৩, জনযুদ্ধ পত্রিকার প্রতিবেদন
“তমলুকের নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল থানা, কাঁথি মহকুমার শতকরা ৮০/৯০ অনাহারী। এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়াছে। ৩টি গ্রামে একদিনে মৃত্যু সংখ্যা ২৩৭। একটি গ্রামের হিসাবে মোট ৩৬৫ জনের মধ্যে ২০২ জন লোক মারা গিয়েছে। দলে দলে লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতেছে। এমন কি লঙ্গরখানায় খাইতে যাইবার লোকও নাই। আবাদী জমির শতকরা ৭০ ভাগ জমি অনাবাদী আছে, আবাদী জমির ফসল তুলিবার লোক নাই। ইহার উপর বন্যায় পাঁশকুড়া থানা, কাঁথির ৪টি থানা, ঘাটালের একটি অংশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। ফসল নষ্ট হওয়া ছাড়া শতকরা ৫০টি গরু নষ্ট হইয়াছে। জমির উপর বালু জমিয়া পুনরায় আবাদের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।
মেদিনীপুর শহরে প্রায় ৮০০০ বুভুক্ষু জমায়েত হইয়াছে, ইহাদের কোন আশ্রয় নাই। দৈনিক গড়ে ৫/৬ জন মারা যাইতেছে। মেদিনীপুরের ৬টি শহরের এইরূপ অবস্থা”
—মন্বন্তর সম্পর্কে সমকালের পত্রপত্রিকায় এরকম অজস্র খবর আছে। যার প্রতিফলন পড়ল সমকালের কবি নাট্যকার কথাকারদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটকে। সমাজের Real ground-এর প্রতিচ্ছবি উঠে এল সাহিত্যে।
এমনই সামাজিক পটভূমিতে বাংলা নাটকে একেবারেই অন্যধারার নাটক নিয়ে এগিয়ে এলেন সাংবাদিক ও ‘ মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮)। বিজন ভট্টাচার্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অর্থাৎ ১৯৪৩-এর এক রাজনৈতিক ও সমাজ পটভুমিকে বেছে নিলেন নাট্যচর্চার ক্ষেত্রস্থল হিসেবে। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ ১ এর ভূমিকায় মাননীয় শমীক বন্দোপাধ্যায় প্রসঙ্গত বলেছেন,
“১৯৪৩-এর মহামন্বন্তরের আগেই খাদ্য মজুত করে কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে মন্বন্তরের যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, তারই ছবি আগুন নাটকের কিউয়ে। মন্বন্তর এসে পড়ে জবানবন্দী নাটকে; গ্রাম থেকে শহরে এসে রাস্তায় অনাহারে মৃত্যুও। নবান্ন-এ মন্বন্তর যেন আরো ঐতিহাসিক ব্যপ্তি পায়। মেদিনীপুরে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন, প্লাবন, মন্বন্তর, চালের চোরাকারবার, গ্রাম থেকে শহরে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মিছিল, শহরে রাস্তায় তাদের দিন যাপন, তাদের উপর যৌন আক্রমণ, আবার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধও, শেষে গ্রামে প্রত্যাবর্তন ও গাঁতায় চাষ, ও সেই শেষ পরিণামে একট। অনৈতিক স্বপ্নে বাস্তবোত্তরণ।” [বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ-১, ভূমিকা- শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়]
গণনাট্যের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন ছোটগল্প রচনা করেই। পরবর্তী সময়ে তিনি পথ বদলে চলে এলেন গান ও নাটকের শিল্পীদের দলে। নাট্য জগতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ সেই ছোটগল্পরেই মতই একটু অন্য form-এ লেখা অর্থাৎ একাঙ্ক নাটক ‘আগুন’ (১৯৪৩) লিখে। চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে মহামস্বান্তর। তেমনই প্রেক্ষাপটে ক্ষুধার্ত মানুষের পেটের জ্বালাকে নিয়ে তিনি লিখলেন ‘আগুন’। বলাবাহুল্য, পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিজনবাবু লিখেছিলেন পরপর তিনটি নাটক—’আগুন’ (১৯৪৩), ‘জবানবন্দী’ (১৯৪৪), ‘নবান্ন’ (১৯৪৪)। ‘আগুন’ (১৯৪৩) নাটকটি ‘অরণি’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ এর ২৩ এপ্রিল। ঐ বছরই মে মাসে নাট্যভারতী মঞ্চে গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় ও নাট্যকারের স্বয়ং নির্দেশনায় অভিনীত হয়। ‘আগুন’ সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজনবাবু বলেছিলেন,
“এই শহরের উপর যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ছায়াপাতের একটা লক্ষণ দেখেছিলাম কিউইং-এর মধ্যে—জলের কিউ, চালের কিউ। র্যাশন বয়-দের যেন একটা শ্রেণিই গড়ে উঠেছিল। এই ব্যাপারটা নিয়েই খণ্ড খণ্ড কয়েকটি চিত্র রচনা করেছিলাম।” [বহুরূপী, ‘নবান্ন’ জুন ১৯৭০ স্মারক সংখ্যা (দ্বিতীয় সংকলন)]
‘আগুন’-এ পাঁচটি দৃশ্যে এসেছে খাদ্যাভাবে বাংলার বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র, উঠে এসেছে অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র। নাট্যকার শহরের উপকন্ঠে বসবাসকারী দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুর্দশাকে বর্ণনা করেছেন এমন করে—চাল সংগ্রহের জন্য র্যাশন দোকানের সামনে অপেক্ষারত বহু মানুষের লাইন। সেই কোন কাকভোরে এসে এরা দু’টো চাল পাবার আশায় লাইনে অপেক্ষারত। প্রথম দৃশ্য থেকেই র্যাশনে চাল ধরার প্রসঙ্গে লাইনে দাঁড়ানোর তৎপরতা রয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যেও তাই স্বামী স্ত্রী সন্তান সবাই চলেছে চাল ধরার উদ্দেশ্যে কন্ট্রোলের লাইনে। আবার অন্নাভাবে স্বামী সতীশ ও স্ত্রী ক্ষিরির পারিবারিক অশান্তির চিত্র উঠে আসে। অভাবের সংসারে কারখানার শ্রমিক সতীশকে তার স্ত্রী ক্ষিরি গঞ্জনা দেয়—”পরণে নেই কাপড়, পেটে নেই ভাত, বড় সুখেই রেখেচো। আবার লম্বা চওড়া কথা! লজ্জা করে না।” নিরুপায় স্বামী-স্ত্রীর এই গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে প্রহার করে। অর্থাৎ এ কাহিনী থেকে সুস্পষ্ট—অভাব-অনটন সংসারের সুখ শান্তি যেমন করে কেড়ে নেয়—তারই দৃষ্টান্ত । নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে রেশন দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন প্রসঙ্গ এবং পঞ্চম দৃশ্যে ‘কন্ট্রোল লাইন’ প্রসঙ্গ। সিভিক গার্ডের অন্যায় অত্যাচার ও অবশেষে চতুর্থ পুরুষ দ্বারা প্রতিবাদ। লাইনে কলহ মুহূর্তে এক যুবকের আর্তনাদ ‘আগুন! আগুন!’। কিসের আগুন–কোথায় আগুন, নানা প্রশ্নের উত্তর (হাতজোড় করে) যুবকটি দেয়- ‘আগুন! আগুন! জ্বলছে আমাদের পেটে।’ ক্ষুধার জ্বালায় রেশনের চাল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জাতির মানুষ জমায়েত হয়েছে কন্ট্রোল দোকানের লাইনে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবারই এক উদ্দেশ্য—দু’মুঠো অন্নের প্রত্যাশা। তাইতো তেল চুপচুপে নাদুস নুদুস চেহারা দোকানি কণ্ঠে শোনা যায়—
“বাব্বা! লুঙ্গি, টিকি, পৈতে, টুপি সব একাকার হয়ে গেছে। আর কি উপায় আছে। ব্যবসার সুখ এই গেল। ওরে পঞ্চা, নে বস্তা কেটে চাল ঢাল চটপট।”
এভাবে চোরাকারবারিদের প্রতিক্রিয়া-নাট্য লক্ষ করা যায়। এমনি করে নাটকে খণ্ড খণ্ড চিত্রের সাহায্যে তৎকালীন জীবনের অন্নসংকটের চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন।
এরপর পঞ্চাশের মন্বন্তরে পটভূমিতে নাট্যকার লিখলেন ‘জবানবন্দী’ (১৯৪৪)। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার এক অভাবী পরিবারের চিত্র উঠে এসেছে ‘জবানবন্দী’ নাটকে। খুব ছোট নাটক। কোন অঙ্ক ভাগ নাটকে নেই। সর্বমোট চারটি দৃশ্যে নাটক শেষ হয়েছে। সর্বমোট ৯টি চরিত্র আছে নাটকে। ‘মাখাল’ গ্রামের সম্পন্ন চাষী পরাণ মণ্ডল ও তার স্ত্রী। পরাণের দুই ছেলে বেন্দা ও পদা। বেন্দার স্ত্রী ও শিশু পুত্র মানিক। গ্রামের প্রতিবেশী রাইচরণ, রমজান ও হাসি, এছাড়া শহরের ভদ্রলোক ও এ.আর.পি. কর্মচারিরা রয়েছে নাটকের চরিত্রগুলিতে।
বৃদ্ধ চাষী পরাণের সংসার বিধ্বস্ত হবার করুণ কাহিনী নাট্যকার তুলে ধরেছেন। চারটি দৃশ্যে বৃদ্ধ পরাণের পরিবার জীবনের ধাপে ধাপে চরম সর্বনাশের কাহিনী উঠে এসেছে। মাথাল গ্রামের সম্পন্ন চাষী অভাবের তাড়নায় আজ অসহায় অবস্থায় শুধু বাঁচার আশায় ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়াসে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বাধ্য হয়। শহরে ঠিকানা তাদের ফুটপাত। অজ পাড়া গাঁয়ে বসবাস পরাণের। অসুস্থ পরাণ। সংসারে খাদ্যাভাব। বেন্দার শিশু পুত্র মানিক খেতে না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করে। মানিকের কাকা পদা তাই বলে,
“মানুষির বাচ্চা তো। সময় মত না পায় দুটো খাতি, না পায় এটা কিছু। এতো আর জন্তু জানোয়ারের বাচ্চা না। সইতি পারে কখনও এত ধকল ঐ অটটুকখানি ছেলে? রোজ তিন বেলা করি জ্বর আসতেছে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। শরীলির আর দোষ কি। বেঁচে যে আছে এখনও এই ঢের।”
ক্ষুধার জ্বালায় গ্রামের আশে পাশে মৃত্যুর খবর আসে। তাদের গ্রামের গ্যাদা গলায় দড়ি দিয়েছে। ছেলে বউ সব মরবে এবার না খেয়ে। গ্রাম যে শ্মশানে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে সিদ্ধান্ত শহরে যাবার। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ পরাণ হাউমাউ করে কেঁদে বলে- ‘আমার সুখির সংসার। হায় পরমেশ্বর!’ এরপর শহরে এসে ফুটপাতে চট দিয়ে খেলাঘরের মত একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করে। পরাণ এখন শহরের ফুটপাতের অনভ্যস্ত ভিখারি। ভদ্রলোকদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে নিরাশ হয়ে পরাণ বড় আঘাত পায়। খাদ্য সংগ্রহ করে তার পরিবারের সকলে যখন তাদের বাসায় ফেরে দেখা যায়, ক্ষুধার জ্বালায় বেন্দার মা তার পাওয়া খিচুড়ি এক নিমেষে গোগ্রাসে সব শেষ করে ফেলে তার আপনজনদের কারো কথা সে মুহূর্তে ভাবার অবকাশ ছিল না। ক্ষুধার্ত শিশু মানিক (বেন্দার পুত্র) খিদে পেটে খিচুড়ি খেয়ে সহ্য করতে না পেরে পেটের যন্ত্রণায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ক্ষুধার জ্বালায় বেন্দার স্ত্রী শহরে এসে চরিত্রদোষে দুষ্ট হয়েছে। শহুরে বাবুর প্রলোভনে পড়ে নতুন শাড়ি পেয়েছে। গভীর রাতে তার সঙ্গে অন্যত্র সঙ্গ দিতে গিয়েছে—শুধু পয়সার বিনিময়ে। এসব শুনে, দেখে বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার স্ত্রী জল দিতে চাইলে সে বিরক্ত হয়ে বলে- “তুই যা, তুই যা। তোর মানুষ মনুষত্ব একেবারে গেছে। তুই আর মানুষ নেই রে বেন্দার মা, তুই আর মানুষ নেই।” অবশেষে পরাণ অসুস্থ হয়ে যায়। পুরানো স্মৃতিতে আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলে—’আমার ঘর, আমার জমি, আমার ছেলে। আমার হাল লাগল, আমার বলদ, আমার সোনার ধানের ক্ষেত, বেন্দার মা, বেন্দার মা!!।” একদিকে অসুস্থ পরাণ মণ্ডল অন্যদিকে ভদ্রলোকের ইশারায় বেন্দার স্ত্রী রাতে সবার চোখের অলক্ষে চলে যাওয়া-এ এক দারুণ যন্ত্রণার চিত্র। বেন্দার যেন মনে হয় – ‘ঐ সেই পরমেশ্বর আর এক ভদ্দরলোকে। সর্বনাশ করে ছাড়লে একেবারে আমাদের।’ পরিবেশে বেন্দার স্ত্রী হয়ে গেল ‘চাষীর ঘরের কলঙ্ক’। অবশেষে বৃদ্ধ চাষী পরাণের মৃত্যু। মৃত্যুর পূর্বে পরাণ শুধু এই কথাটাই বলে যায়।”
“তোরা সব ঘরে ফিরে যা বেন্দা। ঘরে ফিরে যা। আমার, আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক’খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিড়ি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। ফিরে যা। ফিরে যা।”
অবশেষে পরাণ মণ্ডলের মৃত্যু। তার পরিবার আবার গ্রামে ফিরে যাবার সংকল্পে- পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চুপ হয়ে দূরে তাদের গ্রামের দিকে যেন মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।
‘নবান্ন’ (১৯৪৪) নাটকে এই পরিসর আরো ব্যাপক। বস্তুতঃ এ নাটক ‘জবানবন্দীর’ সম্প্রসারিত রূপ। সর্বমোট ৪টি অঙ্কে ১৫টি দৃশ্যের বড় মাপের কাহিনীতে ‘নবান্ন’ নাটকের শেষ হয়েছে। সেখানেও গ্রাম থেকে শহরের আসার করুণ কাহিনী। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ অভাবের তাড়নায় শুধু এক মুঠো অন্নের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার সংকল্প গ্রহণ করে।
নাট্যকার দেখিয়েছেন, মেদিনীপুরের আমিনপুর নামক একটি গ্রামের চাষী প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের দুঃখ দৈন্যের কথা। এ নাটকে শুধু মন্বন্তর ও তার আকালের কথা নয়, তার সঙ্গে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, বন্যা ও বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন ও তার বিপর্যয় উঠে এসেছে। আমরা দেখি, ব্রিটিশের অত্যাচারে প্রধানের দুই পুত্র শ্রীপতি ও ভূপতি এবং স্ত্রী পঞ্চাননীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশের যুদ্ধকালীন ‘পোড়া মাটি নীতি’র প্রকল্পে সাধারণ মানুষের চাল ধান নষ্ট, নৌকা সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি অন্যায় অত্যাচারের প্রসঙ্গ রয়েছে। গ্রাম ও শহরের সুদখোর পাইকার, মহাজন ও জোতদারদের অসৎ আচরণ ও অসৎ ব্যবসার চক্রে পড়ে অসহায় চাষীদের দুরবস্থার চিত্রও উঠে এসেছে। গ্রামের চাষীদের কাছ থেকে নানা কৌশলে অল্প পয়সার বিনিময়ে পাইকাররা চাল ধান কিনে শহরে চালান দেওয়া ও শহরে মজুতদার – গুদামজাত করে কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্য সংকট, বাজার দর বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গ নাটকে আছে। শহরের মানুষের উদাসীনতা, মজুতদারদের দালালি, দালালের লোভী আচরণ, সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারদের নির্মম আচরণ ইত্যাদি করুণ কাহিনী ‘নবান্ন’ নাটকে এসেছে। সব মিলিয়ে ‘নবান্ন’ নাটকে সমকালের মন্বন্তর ও ব্রিটিশ রাজরোষের প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে।
“নবান্ন” নাটকে মন্বন্তরপীড়িত দরিদ্র চাষীদের গ্রাম থেকে শহরে যাত্রার শহর বাসের করুণ অভিজ্ঞতা এবং অবশেষে গ্রামে ফেরার কথা নাট্যকার তুলে ধরেছেন। সুতরাং বলা যায়, মন্বন্তরের এক অন্যতম দলিল ‘নবান্ন’। ‘নবান্ন’ চার অঙ্গে পনেরটি দৃশ্যে বিভক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এখানে একদিকে বর্ণিত হয়েছে এক মন্বন্তর পরিস্থিতি তারপর—মন্বন্তরের পূর্ণাবস্থা ও মন্বন্তর পরবর্তী ছবি। বলাবাহুল্য, ১৯৪৩-এর মেদিনীপুর অঞ্চলের ভয়াবহ বন্যা হয়ে যাওয়া ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য যা কিনা আলোচ্য নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে।
নাটকে সূত্রধার আমিনপুরের চাষী প্রধান সমাদ্দার। এছাড়া আছে প্রধানের দুই ভাইপো কুঞ্জ ও নিরঞ্জন এবং তাদের স্ত্রী রাধিকা ও বিনোদিনী। আর আছে কুঞ্জের একমাত্র শিশুপুত্র মাখন। প্রধানের দুই পুত্র শ্রীপতি ও ভূপতি পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছে। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানোর আন্দোলনে সামিল হয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছে। প্রধানের আপনজন বলতে এখন এরাই। আর আছে প্রতিবেশি দয়াল মণ্ডল অন্য চাষীরা প্রমের সুদখোর মহাজন হারু দত্তের দুরভিসন্ধিতে পয়সার অভাবে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার উপক্রম। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল না ফলায় গ্রামের চাষীরা অভাবের তাড়নায় বিপর্যস্ত। শুরু হল অভাব অনটন–খাদ্য সংকট, অর্থ সংকট। সুযোগ সন্ধানী সুদখোর মহাজন হারুদত্ত সেই সুযোগে কুঞ্জ বা প্রধান সমাদ্দারকে সর্বস্বান্ত করে দিতে চায়। উপায় অবলম্বনহীন হয়ে তারা হারুদত্তের কাছে সংসারের শেষ সম্বল বাসন-কোসনটুকুও বিক্রি করতে বাধ্য হয়। খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগে তার কুঞ্জের একমাত্র সন্তান মাখনও মৃতপ্রায়। অভাবের তাড়নায় সংসারে ভুল বোঝাবুঝি করে নিরঞ্জন গ্রাম ছেড়ে একা শহরে চলে যায় উপার্জনের চেষ্টায়।
এক সময় প্রধান নিরন্ন চাষ। দয়াল মণ্ডলকে গ্রাম ছেড়ে না যাবার পরামর্শ দেয় কিন্তু অবশেষে পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে গ্রামের জমি জায়গা বাড়ি ছেড়ে শুধু বাঁচার প্রচেষ্টায় একমুঠো ভাতের আশায় শহর মুখে যাত্রা শুরু করতে হয়। কেননা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মৃত্যু এবং অবশেষে ঝড়-ঝঞ্ঝা জলোচ্ছ্বাস প্রধান সমাদ্দারদের পথে নামিয়েছে। তাই নাট্যকার বলছেন—*ঘরই এবার পথে নেমে এসেছে। (১/৩)
শহরের ফুটপাতে প্রধানত কুঞ্জের পরিবার। শহরে কালোবাজারির বাড়- বাড়ন্তের ছবি অতি সহজে চোখে পড়ে। অসাধু ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়া তার গুদামে মজুত করেছে প্রচুর ধান চাল। সাধারণ ক্রেতা গেলে হাত-উলটে নেই নেই সুর। ধনবানদের জন্য চড়া দামে সমস্ত মজুত চাল চিনি সহজলভ্য হয়ে রইল। অথচ এই মন্তন্তরের কালে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মরছে। আঁস্তাকুড়ে পশু মানুষ যকত্রে খাদ্য অন্বেষণ করছে। এমনকি ডাস্টবিনে কুকুরে-মানুষে খাদ্যের লড়াই। অভুক্ত কুঞ্জ ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করেছে বাবুদের ভোজ বাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবার পাবার আশায়। অবশেষে কুকুরের কামড়ে হাত দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। এমন দুঃসময়ে শুধু পাশে স্ত্রী রাধিকার সান্ত্বনা হচ্ছে না। জল এনে দেব, একটু জল। জল খাবে!’ – খুব যন্ত্রণা।
এছাড়া মন্বন্তরে খাদ্য ঔষধ পথ্যের অভাবে বিনা চিকিৎসায় কুঞ্জ হারিয়ে ফেলে তার একমাত্র পুত্র মাখনকে। শহর কলকাতার ফুটপাতে নারী পাচারকারী দালালদের হাতে পড়ে যায় বিনোদিনী। ব্যবসায়ী হার দত্ত সরল অভাবী গ্রাম্য মেয়েদের কাজ দেবার নামে অল্প পয়সায় কিনে এনে শহরে বিক্রি করে দেয়। অপরদিকে আছে পেটে ক্ষুধার জ্বালা। ক্ষুধার জ্বালায় লঙ্গরখানায় খিচুড়ি পাওয়ার আশায় শহরের রাস্তায় ঢল নেমেছে। কিন্তু গ্রাম থেকে যত মানুষ শহরে এসেছিল বাঁচার আশায়-তাদের সবার বাঁচা হল না। অনেক মানুষ ফুটপাতে খিদের জ্বালায় প্রাণ হারিয়েছে—কেউ বা আত্মহত্যা করেছে অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। শহর কলকাতা ভিখারির মৃতদেহে ভরে যাচ্ছে। মড়ক লেগেছে—মহামারী দেখা দিয়েছে।
অবশেষে এক সময় আসে গ্রামে ফেরার পালা। যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল প্রাণের আশায়, তারা এই শহরের প্রাণহীন জীবন বৃত্তান্ত বুঝতে পেরে আবার গ্রামে ফিরে যেতে চায়। কেউ ফিরতে পারল কেউ বা পারল না। যারা গ্রামে ফিরল, তারা নতুন করে বাঁচার ‘ও মন্বন্তরে গ্রাম ‘বাংলার দুরবস্থা ও মহাশ্মশানের চিত্র নাট্যকার তুলে ধরলেন ‘নবান্ন’ নাটকে। সমকালে ‘যুগান্তর’ পত্রিকার প্রতিবেদন সেই কথাই বলে—
‘বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায় বাঙলার সেই দুঃস্থ কৃষকদের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্য সত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। (যুগান্তর পত্রিকা : ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৪ )
তথ্যঋণ :
১. পঞ্চাশের মহা মন্বন্তর ও বাংলা ছোটগল্প , মানস মজুমদার।
২. পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, বিনতা রায়চৌধুরী। –
৩. কথাসাহিত্য—মন্বন্তরের দিনগুলিতে, সুব্রত রায়চৌধুরী।
৪. বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ-১ (দে’জ পাবলিশিং) –
৫. গণনাট্যের নবান্ন : পুনর্মূল্যায়ণ, দর্শন চৌধুরী। :’
৬. নাট্যকথা : বিষয় বিজন সম্পাদক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। –
৭. বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত, মন্দিরা রায়।